মোহাম্মদ সাদউদ্দিন:
টিকি আর দাড়িতে যতই আলাদা করার চেষ্টা করুক না কেন, বাঙালির কিছু বৈশিষ্ট তাকে বাঙালি করেই রেখেছে। এই অতি সুন্দর সম্প্রীতির কথা যিনি বলেছিলেন সেই ভাষাতত্ত্ববিদ -জ্ঞানতাপস ড: মুহম্মদ শহীদ্দুল্লাহই হলেন ভাষা আন্দোলনের স্বপ্নপুরুষ ও স্বপ্নদ্রষ্টা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অবিভক্ত ২৪ পরগণার হাড়োয়া থানার পিয়ারা গ্রামের ভূমিপুত্র তিনি। ১৯২০-২১ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তখন ভারতের রাজনৈতিক আকাশ উত্তপ্ত। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ, অহিংস ও খিলাফৎ আন্দোলনের উত্তাল প্রবাহে আচ্ছন্ন ভারত। আর ব্রিটিশ শাসিত সেই ভারতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হবে, না উর্দু হবে তা নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে ছিল বিস্তর বিতর্ক । আর সেই ফাঁকে বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের কিছু কর্মকর্তা তাদের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাদের ডাকা একটি সভায় আমন্ত্রিত ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন , তাতে তিনি প্রমাণ করেন , কেন বাংলা হবে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা? শহীদুল্লাহ সাহেব সেদিনই প্রমাণ করেছিলেন অবিভক্ত বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, বিহারের ছোটনাগপুর সহ বিস্তৃর্ণ এলাকার মানুষ বাংলায় কথা বলেন যা হিন্দী বা উর্দু থেকে বেশি।কিন্তু কথাটা দু:খের আচার্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সেদিন সংস্কৃত ভাষার প্রতি সাওয়াল করলেও তা সভাতে আসা মানুষজন প্রত্যাখ্যানও করেন। শহীদুল্লাহর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ পরবর্তীতে ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ছাপা হয়। আমাদের অতি দূর্ভাগ্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্হ হয়ে গেলেন আর ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষক সহায়ক থেকেও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে চলে গেলেন। কলকাতা তিনি ছাড়তে চাননি, যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহর বেতনটা সামান্য বাড়িয়ে দিত। এই বেতন বৃদ্ধি না হওয়ার কারণেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সহ আরো অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলে যান। ধর্মের ভিত্তিতে শুধু দেশ ভাগ হয়নি ১৯৪৭ সালে। বাংলাও ভাগ হয়ে গিয়ে তার একটি অংশ পাকিস্তানের প্রদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল কখনো পূর্ববঙ্গ বা কখনো পূর্বপাকিস্তান হিসাবে। কায়েদ-ই-জিন্নার বা খাজা নাজিমুদ্দিনের উর্দুই হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ শুধু গর্জে উঠেনি, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো জ্ঞানতাপসরাও সেদিন গর্জে উঠেন। ভাষা আন্দোলনের অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন মহম্মদ তোহা ও গোলাম আজমও। ভাষা আন্দোলনের দুই সংগঠন তামুদ্দিন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রাণপুরুষ ছিলেন ভাষাবিদ-জ্ঞানতাপস ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর ছেলেমেয়েরাও ছিলেন ভাষা আন্দোলনের এক একটি সৈনিক ও সংগঠক। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা তামুদ্দিন মজলিশ ভাষা নিয়ে বিস্তর আন্দোলন করেন। দেশভাগ বা বাংলা ভাগ হলেও পশ্চিমবঙ্গের অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তানরা আত্মীয় বাড়িতে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েও ভাষা আন্দোলন করেন । তাদের কথা আমরা আজ বিস্মৃত। অবশ্যই শহীদুল্লাহ সাহেব ২০-এর দশকেই কলকাতা ছাড়েন। আমাদের খুব দূর্ভাগ্য যে, এইরকম একজন জ্ঞানতাপস ও বিশ্বনন্দিত ভাষাবিদকে আর দুই বাংলাতে সেভাবে স্মরণ করি না। তাঁকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের (তখন অবিভক্ত বঙ্গ) বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পিয়ারা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই। বাংলা সন অনুসারে তারিখটি হয় ২৭ আষাঢ় ১২৯২ বঙ্গাব্দ। আর আরবি সন অনুসারে হয় ১৩০৫ হিজরির ২৬ রমজান। দিনটি ছিল শুক্রবার রাত। মায়ের নাম হরুন্নেসা ও পিতার নাম মফিজুদ্দিন আহমেদ। হাড়োয়ার বিখ্যাত সুফিসাধক সৈয়দ আব্বাস আলী (রহ:) ওরফে পীর গোরা চাঁদের বিখ্যাত খাদেম শেখ দারামালিকে বংশধর এই ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মাতুলালয় ছিল পার্শ্ববর্তী দেগঙ্গা থানার ভাসিলিয়া। ২৪টি পরগণার অন্যতম ২৪ পরগণার বালান্দি পরগণার অন্তর্গত এই পিয়ারা গ্রাম। পীর গোরা চাঁদের আরো এক খাদেম পিয়ার শেখ। উনারই নামানুসারে গ্রামের নাম পিয়ারা গ্রাম। শহীদুল্লাহর বংশধররা লাখেরাজ বা ওয়াকফ সম্পত্তি পেয়ে পিয়ারা গ্রামে বসবাস করতে থাকেন।
মুসলিম সন্তানদের নামকরণ অনুষ্ঠানটির নাম ‘আকিকা’। সেই আকিকার দিনে শহীদুল্লাহ-র প্রথমে নাম রাখা হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহিম। কিন্তু শহীদুল্লাহর মা হরুন্নেসার এই নাম পছন্দ হয়নি। মহরম মাসে হরুন্নেসার গর্ভে এসেছিলেন শহীদুল্লাহ। তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শহীদুল্লাহ যার অর্থ ঈশ্বর বা আল্লাহর নামে উৎসর্গ। ছোটবেলা থেকে দারুণ আত্মভোলা ছিলেন বলে আদর করে সবাই ডাকতেন ‘ সদানন্দ’। সদানন্দ এই ডাক নামটিই ছিল বেশি জনপ্রিয়।
শহীদুল্লাহর পিতা মফিজুদ্দিন আহমেদের চাকুরি ছিল হাওড়ার সালকিয়ায়। শৈশব ও শৈশব শিক্ষা পিয়ারা গ্রামে হলেও দশ বছর বয়সে পিতার কর্মস্হল হাওড়ার সালকিয়ায় চলে আসেন। সেখানকার মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৯ সালে তিনি মিডল স্কুল পাশ করেন খুব ভালো ফল করেই। ১৯০০ সালে তিনি হাওড়া জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সপ্তম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে রৌপ পদক পান। স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে তিনি আরবি বা পার্সির পরিবর্তে তিনি সংস্কৃতি নিয়েছিলেন। এছাড়াও অজানাকে জানা ছিল তার প্রবল ইচ্ছা। সালকিয়া এলাকা বরাবরই ছিল বহুভাষী ও বহু ধর্মের মানুষের বসবাস। তাই স্কুলজীবনেই বহুভাষী বন্ধুদের সঙ্গে মিশে তিনি ৪-৫ টি ভাষাতেই দক্ষ হয়ে যান। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি গণনাও শিখে যান। স্যার উইলিয়াম জোনস ও শ্যামাচরণ সরকারের জীবনী পড়ে তিনি বিভিন্ন ভাষা শেখার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুলে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। প্রতিবেশী হিন্দু মহিলারা এসে শহীদুল্লাহর মা হরুন্নেসার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলতেন , ‘ মা, আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের ছেলেরাও আপনার ছেলের মতো হয়। আপনি রত্নগর্ভা।’
যাই হোক, ১৯০৬ সালে কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় দারুণ ফল করে পাশ করেন। তারপর হুগলী কলেজে(বর্তমানে হুগলী মহসীন কলেজ) সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সুস্হ হয়ে তিনি যশোহর জেলা স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরিতে যোগ দেন। কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ঐ স্কুলে শহীদুল্লাহর ছাত্র। একবছর চাকুরি করার পর তিনি আবার কলকাতায় এসে সিটি কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি এ দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। একজন মুসলিম ছাত্র হিসাবে তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তারপরেও রক্ষণশীলদের চাপে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে এম এ পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। এনিয়ে তখনকার দিনের পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখা হয়। প্রতিবাদও হয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৩ সালে জার্মান যাওয়ার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি পান। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক ছাড়পত্র না পাওয়ায় তিনি জার্মানি যাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। পরে নবাব আলী চৌধুরী শহীদুল্লাহর জার্মানি যাওয়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করায় তিনি ১৯২৬ সালে সে সুযোগ পান। প্যারিস যাওয়ার আগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে সীতাকুণ্ডুর শিক্ষকতা ছেড়ে বসিরহাট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। শহীদুল্লাহ সাহেব সপরিবারে বসিরহাটে থাকতে লাগেন।চার বছর ওকালতি করে ঐ পেশা ভালো লাগেনি। তাই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান ড: দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে গবেষক সহায়ক রূপে নিযুক্ত হন।১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন শরৎকুমার লাহিড়ীর গবেষক -সহায়ক।
যে সময় বঙ্গের মাটিতে কোনো শিশু-কিশোরদের জন্য কোনো ভালো পত্রিকা ছিল না,তখন তিনি ১৯২০ সালেই উনার সম্পাদনায় ‘ আঙুর’ নামে একটা মাসিক শিশু পত্রিকা বের হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করা কালীন তিন কতৃপক্ষকে বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সেভাবে সাড়া দেননি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হলে সেখানকার আহ্বানে তিনি ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার হিসাবে যোগ দেন। আবার একই সময়ে ওখানকার আইনের খণ্ডকালীন অধ্যাপকও হন। দীর্ঘ ৩০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এইসময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৯০৯ সালে আবিস্কার করা চর্যাপদকে সাজান ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । এনিয়ে প্যারিসে যান গবেষণা করতে। ঢাকার পর ১৯৫৪ সালে যোগ দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখান থেকে চলে আসেন বগুড়া স্যার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে
। এখানেই তিনি হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে একটি দাঙ্গা থামান। এই হল শহীদুল্লাহর কর্মজীবন।
এর বাইরেও কলকাতা থেকে ‘আঙুর’, ‘ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’, পরে ‘বঙ্গভূমি’, ‘তকবীর’, ইংরেজি ‘পিস’ ৫ টি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন প্যারিসে সুবার্বণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পার্শী ভাষা তিব্বতী সহ বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭-২৮ সালেই প্যারিসে থাকার ফাঁকে জার্মানীর ফ্রাইবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন থ। দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও স্হানে ভাষাকেন্দ্রিক সেমিনারে যোগ দেন। শুধু তাই নয় অনেক প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬১-৬৪ সাল পর্যন্ত ঢাকার বাংলা একাডেমির ইসলামি বিশ্বকোষের সম্পাদক হন। ১৯৬৩ সালে ‘ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ‘ প্রণয়ন করেন(সম্পূর্ণ বাংলা উপভাষা)। এটি একটি কঠিন কাজ।
এছাড়াও শহীদুল্লাহ একাধিক গ্রন্হ প্রণয়ন করেন।এক একটি অ মূল্য সম্পদ।সেগুলি হল সিদ্ধা কখন পীর গীত ও বৌদ্ধ দোহা(১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা(প্রথম খণ্ড-১৯৫৩, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান(১৯৬০), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত(১৯৬৫), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ(১৯৪৫), ইকবাল(১৯৪৫), আমাদের সমস্যা(১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ(১৯৫৭), Essays on Islam(1945), Traditional Culture in East Pakistan (1965), ধ্বনিতত্ত্ব(মুহম্মদ আব্দুল হাইকে সঙ্গে নিয়ে), রকমারি(১৯৩১), শেষ নবীর সন্ধানে ও ছোটদের রাসুলুল্লাহ(১৯৬২)। এইভাবে তিনি অনুবাদ সাহিত্য সহ ৪০ টি গ্রন্হ রচনা করেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড , বাংলা ভাষা ও গবেষণার জন্য ১৯৬৭ সালেই ‘ প্রাইড অব পারফরমেন্স’ পুরস্কারে ভূষিত করে। ঐ বছর ফরাসি সরকার ‘ নাইট অব দি অর্ডার্স অব আর্টস অ্যাণ্ড লেটার্স’ পদক দেয়।পরবর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাকে মরনোত্তর একুশে পদক দেয়। তিনি যথার্থই একজন ভাষা সাধক ও জ্ঞান সাধক। সেরিব্রাল থম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই এই জ্ঞানতাসে ও বহুভাষাবিদের জীবনাবসান হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্জন গেট ঢুকেই মুছা খান মসজিদের কাছেই আজ তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। তার গবেষণা ও সৃষ্টি আমাদের কাছে পাথেয়।
লেখক সাংবাদিক ও গবেষক

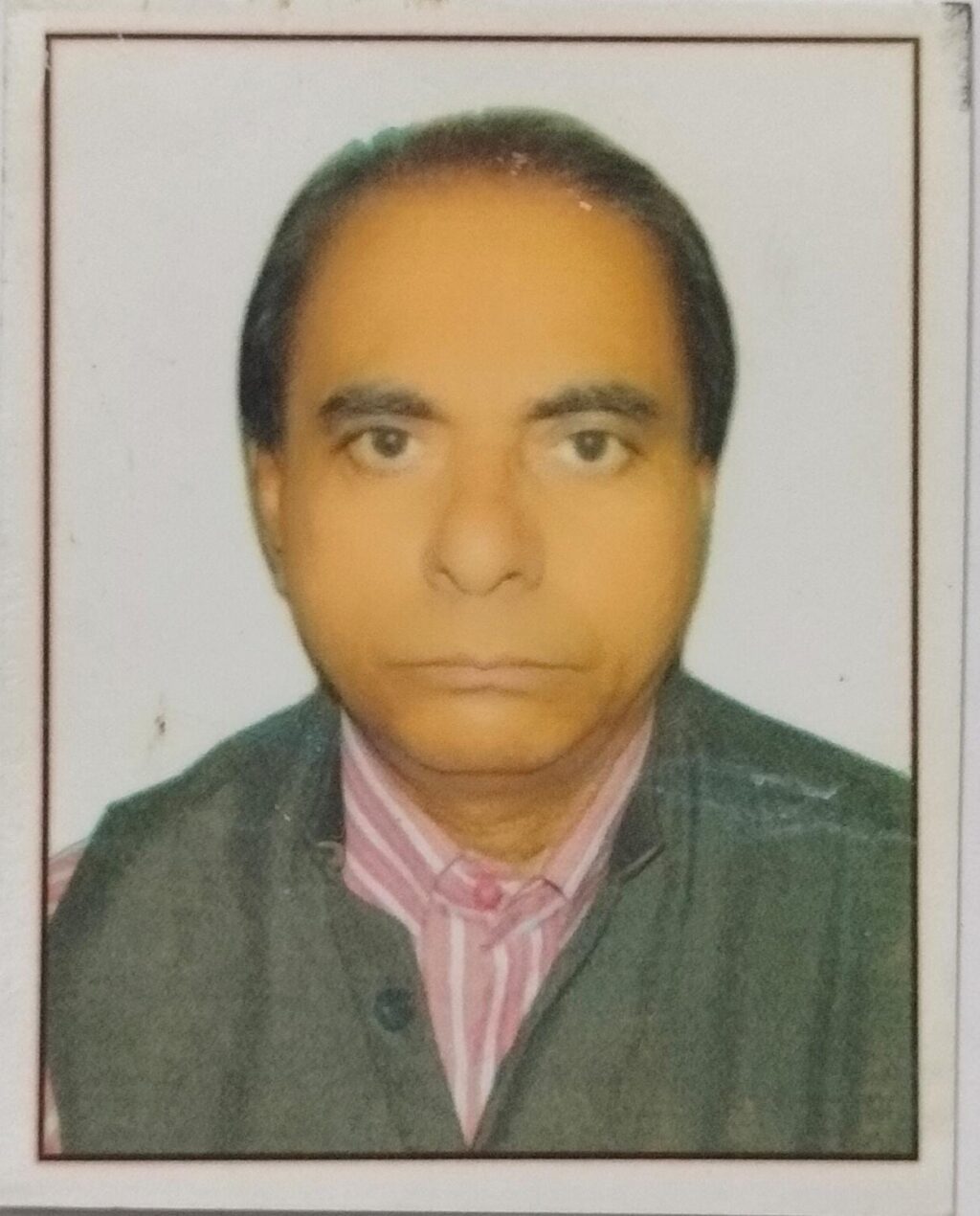
আরও পড়ুন
১৯ বছর পর বাবার কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগ অবরোধ
ওসমান হাদিকে নিয়ে পোস্ট, আসিফ মাহমুদের পেজ সরিয়ে দিল ফেসবুক